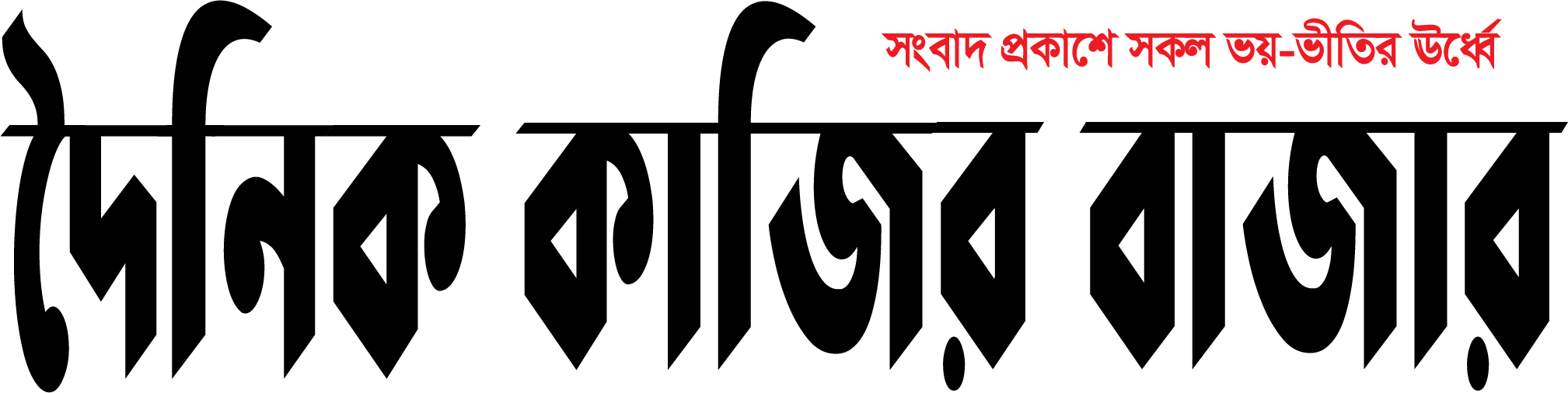কাজিরবাজার ডেস্ক :
আবদুল গাফ্্ফার চৌধুরীর ‘একুশের গান’ কবিতার শেষের কয়েকটি লাইন ‘আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে/ জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে/ দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি/ একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি…।’ ভাষা আন্দোলন নিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে জোরালো দাবি তুলেছিল সর্বপ্রথম তমদ্দুন মজলিস। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ‘সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি’। এই কমিটির সিদ্ধান্তেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়েছিল।
রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে আবুল কাসেম তার এক লেখায় বলেন, ইংরেজরা এক সময় জোর করে আমাদের ঘাড়ে ইংরেজী ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। সেইভাবে কেবলমাত্র উর্দু অথবা বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্বের সেই সা¤্রাজ্যবাদী অযৌক্তিক নীতিরই অনুসরণ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, কোন কোন মহলে সেই চেষ্টা চলছে এবং তাকে প্রতিহত করার জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। সর্বশেষে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে তিনি দাবি করেন, ‘লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা দিতে হবে।
’৪৮ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এমন কি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচয়িতা বশীর আল হেলালও যখন লেখেন ‘তমদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক উদ্যোগই ’৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন বিশেষ গতি লাভ করেছিল।’ তখন বুঝতে কষ্ট হয় না উল্লিখিত চিন্তার শিকড় কতদূর বিস্তার লাভ করেছে। এর প্রমাণ গত তিন চার বছর বিভিন্ন মাধ্যমে তমদ্দুনপন্থীরা বলতে শুরু করেন যে ‘তারাই ভাষা আন্দোলনের জনক’। তাই ঘটনাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণে এসব দাবির যৌক্তিকতা দেখে নেয়া দরকার।
বদরুদ্দীন উমরের লেখা ‘ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ-কতিপয় দলিল’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ভাষা আন্দোলন কেন্দ্র করে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটিতে ৩২ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ছিল। ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে (৯৪ নবাবপুর রোড) এই কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অলি আহাদ ও আরও কয়েকজন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন ও ভোট দেন। সিদ্ধান্তটি গৃহীত হওয়ার পর অলি আহাদ মন্তব্য করেন, কমিটি যে প্রস্তাবই গ্রহণ করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ পরদিন সকালে ছাত্ররা নিজেরাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। একথা শুনে আবুল হাশিম সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মে একটি প্রস্তাব করেন যে পরদিন সকালে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয় তাহলে সেই সঙ্গে সর্বদলীয় কমিটি বিলুপ্ত হবে। এই দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী শামসুল হক, আজিজ আহমদ ও কাজী গোলাম মাহবুবকে দায়িত্ব দেয়া হয় পরদিন সকালে ছাত্রদের কাছে সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করার ও তাদের ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা থেকে বিরত রাখার চেষ্টার জন্য। পরদিন সকাল সাড়ে আটটার দিকে ৯৪ নবাবপুর রোডের আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। অলি আহাদ তখন সেখানে উপস্থিত হয় এবং জানান যে, একটা দোকানের সামনে থেকে পুলিশ এক পিকেটারকে গ্রেফতার করেছে। সাড়ে নয়টার দিকে অলি আহাদ আবার ওই অফিসে গিয়ে খবর দেন যে ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে বহু ছাত্র সমবেত হয়েছে। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হওয়া ও গুলিবর্ষণের পর সর্বদলীয় কমিটির কোন প্রভাব আর থাকেনি। বরং তাকে বিলুপ্ত বলেই ধরে নেয়া হয়েছিল।
বদরুদ্দীন উমর তার ‘পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি-১’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ ‘পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি’ গঠন করা হয়। মওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের দিয়ে গঠিত এই কমিটির সদস্য ছিলেন সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ, প্রাদেশিক মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, ড. আবদুল মোতালেব মালিক, ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন, এমএলএ মৌলানা অবদুল্লাহ আল-বাকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, দৈনিক আজাদ সম্পাদক এমএলএ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (পূর্ব বাঙলা সরকার-ঢাকা), পূর্ব বাঙলা সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি মীজানুর রহমান, সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাজউদ্দিন আহমদ, ইসলামী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক শইখ শরাফউদ্দিন, একই কলেজের অধ্যাপক একিউএম আদমউদ্দিন, চট্টগ্রামের আলাবিয়া প্রেসের স্বত্বাধিকারী মওলানা জুলফিকার আলী, ঢাবির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গণেশ চন্দ্র বসু, মোহিনী মোহন দাস ও গোলাম মুস্তফা।
এদিকে, তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত পুস্তিকাদি ও প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাসেম ও তার সহযোগীদের বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত বক্তব্যে দেখা যায়, তাদের লক্ষ্য ছিল দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা চালানো। এরা রাজনৈতিক চিন্তায় প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সম্ভবত রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিষয়টিকে তাদের এই বিশেষ প্রয়োজনের অংশ হিসেবেই তারা চেয়েছিলেন। বাঙালী জাতিসত্তার সঙ্গে সমন্বয় করে নয়। মতাদর্শগত এই বৈশিষ্ট্যর কারণ তারা ভাষা আন্দোলনে আপোসপন্থা গ্রহণে দ্বিধা করেননি। এর প্রমাণ মার্চে জিন্নাহর পূর্ববঙ্গে সফর উপলক্ষে ভাষা বিষয়ক লক্ষ্য অর্জনে তাদের আনন্দ ও প্রত্যাশা এতই স্পষ্ট ছিল যে কোন দূরদর্শিতার পরিচয় না রেখেই লীগ শাসনের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে তারা মাঝপথে আন্দোলন স্থগিত করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। এমন কি জিন্নাহ চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য অর্জনে চূড়ান্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও ওই স্থগিত আন্দোলন শুরুর কোন উদ্যোগও তারা গ্রহণ করেননি। সংগ্রাম পরিষদকে উজ্জীবিত করার কোন চেষ্টাও তারা করেনি। তমদ্দুন মজলিসের এই ভূমিকার পরও ভাষা আন্দোলন নিয়ে আরও অনেক ঘটনা প্রবাহ চলতে থাকে।
সে সময় পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড প্রাদেশিক ভাষাগুলোর জন্য আরবি হরফের যে সুপারিশ করেছেন একমাত্র বাংলার ওপরই তার আঘাত তীব্র ও ব্যাপকভাবে পড়বে। পাঞ্জাবী, সিন্ধি, ব্রাহুই, বেলুচি, পশতু ও বাংলা পাকিস্তানের সব প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলাই সাহিত্য সম্পর্কে ভাব ঐশ্বর্য্য,ে প্রকাশভঙ্গির উৎকর্ষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর অন্যতম। অন্যান্য সাহিত্যে কোন চর্চা নেই বর্তমানে এই মৃতকল্প ভাষাগুলো উর্দু হরফেই লিখিত হচ্ছে। কাজেই হরফ বদলের আঘাত পাকিস্তানের সর্বপ্রধান ও অধিক সংখ্যক লোকের ভাষা বাংলার ওপরই পড়বে। অনভিজ্ঞ ও মূর্খ লোকেই শুধু বলতে পারে হরফ পরিবর্তনে ভাষার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।
কার্জন হলে সমাবর্তন বক্তৃতায় জিন্নাহ যখন রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সেই পুরনো সুরেই কথা বলেন, তখন উপস্থিত ছাত্রদের থেকে ‘নো নো’ ধ্বনির প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো। তখন জিন্নাহ কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার বক্তব্য দ্রুত শেষ করে চলে যান। বিদায়ের সময় প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি বেশ জোরেশোরেই উল্লেখ করেন। কার্জন হলে ওই ‘নো নো’ প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন ও তার সহকর্মী ছাত্ররা।
একই দিন সন্ধ্যায় জিন্নাহ সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি শামসুল হক, কমরুদ্দিন আহমদ, আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এরপরও প্রতিনিধিদল সঙ্গে নেয়া স্মারকলিপিটি পেশ করতে ভুলে যায়নি। ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক রচিত ‘ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য’ গ্রন্থে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। একই গ্রন্থে বলা হয়েছে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণেতা বদরুদ্দীন উমরের মতে ঢাবির রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয় ’৫১ সালের ১১ মার্চ। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন ১৯৫২ সালের ১৩ মার্চের পর কোন একসময় পতাকা দিবস পালিত হয়, তাতে ৭৫০ টাকা গৃহীত হয়েছিল।
বায়ান্নর ৪ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচী সফল করে তোলার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যুবলীগ কর্মীরা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এদের ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় সাড়া দেয় ঢাকার প্রতিটি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রদের ওই সভা থেকে সারাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল, ছাত্রধর্মঘট ও মিছিলসহ আইন পরিষদ ঘেরাওয়ের প্রস্তাব করা হয়। কারণ ও দিন পূর্ববঙ্গে আইন পরিষদের অধিবেশন চলার কথা ছিল।
পাকিস্তানীরা বাংলাকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভাষার আজ বড় নাজুক দশা। আমরা খুব অবহেলা করেই ভুলতে বসছি সেই প্রিয় বাংলাকে। একুশে ফেব্রুয়ারির সব আবেদন ও ভাবনা যখন একদিনের আয়োজনে সীমিত হয়ে আছে। সারাবছর ধরে অশুদ্ধ বাংলা বলার উৎসব হবে তা আর বিচিত্র কি? কেন আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না সাজানো এই গ-ি থেকে? ভাষা আন্দোলনের এত বছর পরও বাংলা নাটক, সিনেমাসহ শিল্প সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাংলাভাষার অপব্যবহার হচ্ছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলনের সূচনা, বুকের রক্ত ঢেলে জাতিকে রুখে দাঁড়াবার সাহসে উজ্জীবিত করেছিল যারা, সেই ভাষা শহীদ স্মরণে জাতীয় শোক দিবস পালিত হবে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার মধ্যে সীমিত থাকেনি, ভাষাভিত্তিক চেতনায় জাতি ক্রমে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সোচ্চার হয়। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনের শিকল ছিঁড়ে মুক্তিকামী মানুষ একুশের চেতনার পথ ধরেই একাত্তরে রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম করে। আজ বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি দেশ একটি পতাকা রয়েছে। আধা শতাব্দীর এই দেশটি এগিয়ে যাচ্ছে।